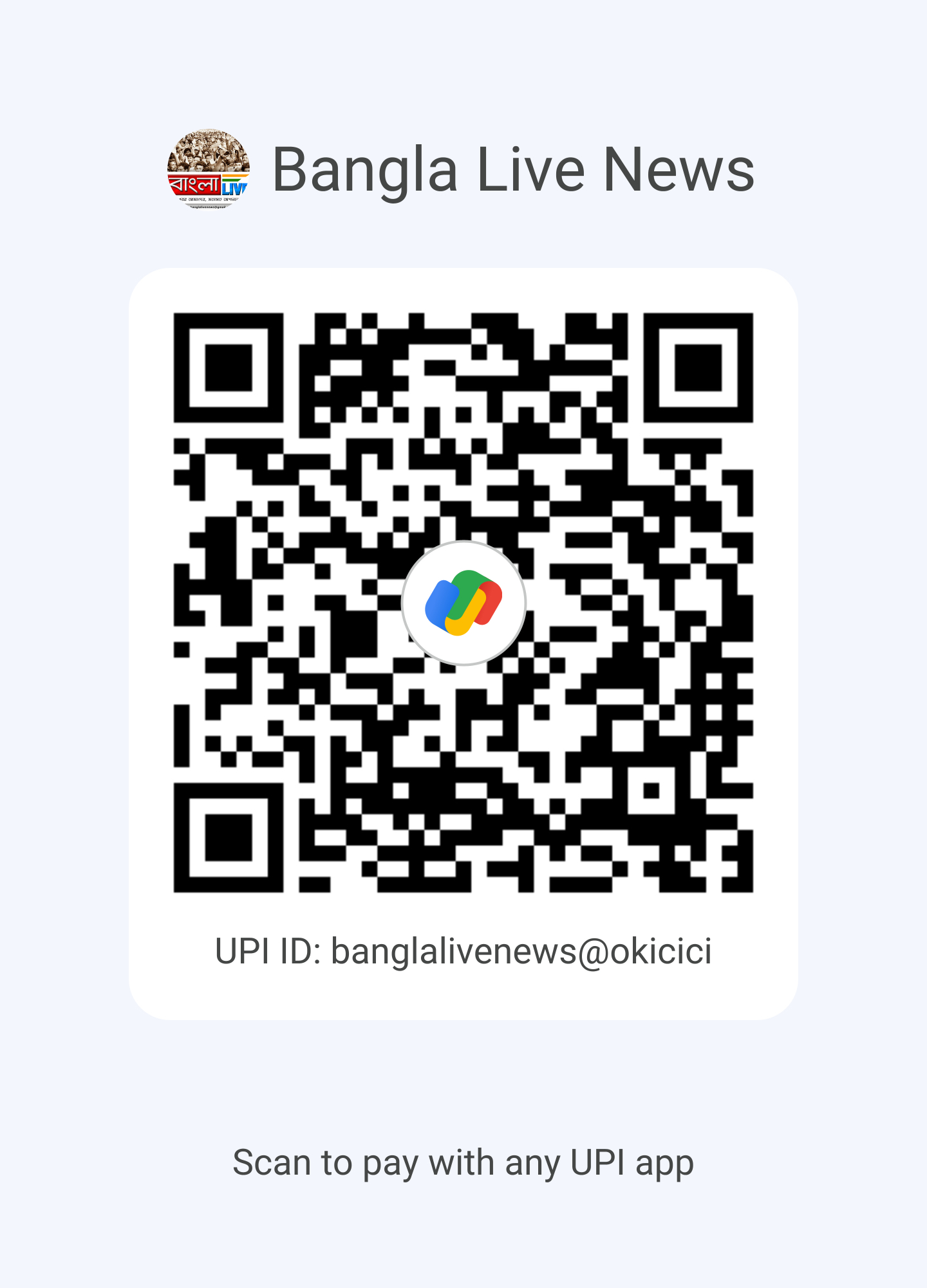কালীঘাট মন্দিরের ইতিবৃত্ত

কলকাতাতে অনেক ধর্মীয় স্থান আছে। কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীন হল কালীঘাটের কালী মন্দির।
যাঁরা কলকাতায় বেড়াতে আসেন বা থাকেন তাঁরা কেউই কালীঘাট মন্দির দেখেন নি এমন হয় না। মায়ের ভক্তরা বিশ্বাস করে যে কালী ঠাকুর কখনও তাঁর ভক্তদের খালি হাতে ফেরান না।
তবে কালীঘাটের কালী মন্দির কবে সৃষ্টি হল সে ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় নি।
পৌরাণিক ( পীঠমালা তন্ত্র) কিংবদন্তী অনুসারে, সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিহ্নিত দেহের সতীর ডান পায়ের চারটি (মতান্তরে একটি) আঙুল এই কালীঘাট তীর্থে পড়েছিল।
জনশ্রুতি যে বল্লাল সেনের সময় (১১৫৯-১১৭৯ খৃঃ) এই জায়গাটি কালীক্ষেত্র নামে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর আমলে তীর্থ দর্শনের আশায় অনেক পুন্যার্থী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কালীক্ষেত্রে স্নান করতে আসতেন।
সেই সময় এই কালীক্ষেত্র বহুলা (বেহালা?) থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যিখানে ত্রিভুজাকৃতি ৩ কিলোমিটার জায়গাকে অতি পবিত্র বলা হত।
ত্রিভুজের তিন কোণে ছিল ব্রহ্মা, বিষনু ও মহেশ্বরের মন্দির। এই কালীক্ষেত্র সীমার মধ্যে কোন এক জায়গায় সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে সতীদেহের পায়ের আঙুল পড়েছিল। সেই জন্য সেখানে এক দেবীমূর্তি ও একটি ভৈরব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর আর দেবীমূর্তি কালী।
কোনো কোনো গবেষক বলেন “কালীক্ষেত্র” কথাটি থেকে “কলকাতা” নামটির উদ্ভব। এটাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরানিক ইতিহাস। কালীঘাটের আদি সৃষ্টির ইতিহাস পুরোটাই কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে। ।
আগে কালী ছিলেন অনার্যদেবী। তখনও তিনি হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে পুরোপুরি ঠাঁই পান নি। কালীর পূজো পুরনো বিশ্বাস অনুযায়ী নর ও অন্যান্য বলি দিয়ে করা হত। তাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল কালীক্ষেত্রের এই দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ এলাকায় যেখানে তখন আইনের শাসন ও সভ্যতার আলো এসে পৌঁছয়নি।
এই অঞ্চলের অধিবাসী তখন প্রধানত পোদ, জেলে, দুলে,বাগদী প্রভৃতি আদিবাসী। কিছু তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ তীর্থ যাত্রী গোপনে পূজো দেবার জন্য এখানে আসতেন।
এরপর থেকে ৩০০ বছর কালীঘাট বা গঙ্গার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।
এরপর কালীঘাট সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া গেল ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের রচিত ‘মনসা মঙ্গল’ কাব্য থেকে। জানতে পারছি কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট সম্বন্ধে কিছু কথা। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী ভাগলপুর থেকে সাগরের দিকে চলেছে।
তরী বাইতে বাইতে কয়েকদিন বাদে নানা গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে তাঁরা পৌঁছলেন চিৎপুরে। দুপুরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বেতড়ে (বর্তমান শিবপুর) পৌঁছলেন। এখানে রয়েছে বেতাই চন্ডীর প্রাচীন মন্দির। এখানে চাঁদ সওদাগর পূজো দিয়ে ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম করে আবার নদী পেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে কালীঘাটে থামলেন। বণিক কালিঘাটে মায়ের পূজো দিলেন।
এর কয়েক বছর পরে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবত ছত্রভোগে অম্বুলিম্বঘাট দর্শন করে পুরীতে যান। চৈতন্য ভাগবতে ছত্রভোগ থেকে জলপথে পুরী যাবার বর্ণনা নেই। চৈতন্যদেব যদি সত্যি ছত্রভোগ থেকে পুরী গিয়ে থাকেন তবে বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল অম্বুলিম্বঘাট থেকে । পথে পড়েছিল বাড়ুইপুর, গড়িয়া বোড়াল ইত্যাদি গ্রাম। নৌকো পেরিয়ে যাচ্ছে কালীঘাট । একটু দূরে নৌকো এসে পৌঁছল মুন্সীগঞ্জের কাছে। এখান থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে গঙ্গা সোজা বয়ে গেছে কলকাতা চিৎপুর গ্রাম হয়ে হুগলীর দিকে। বাঁদিকে সংকীর্ণ খাড়ি বা খাল। তারা এখানে খাল পেরিয়ে মেদিনী পুর হয়ে পুরী যান। শ্রীচৈতন্যদেব শাক্ত তীর্থ কালীঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।
বেশ বোঝাই যাচ্ছে ৫০০ বছর আগে থেকেই ঐতিহাসিক তথ্যে কালীঘাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।
তখন হুগলী নদী বা গঙ্গা বর্তমান প্রিন্সেপ ঘাটের বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, বৈষবঘাটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যাধরী নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশতো।
গঙ্গা ছিল বিশাল চওড়া ও গভীর। ঘন নিবিড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিপুল জলধারা প্রবাহমান ছিল। এটাই ছিল তৎকালীন বঙ্গোপসাগরে যাবার জলপথ। তখন গঙ্গা প্রবাহিত হত কালী মন্দিরের পাশ দিয়ে। এই পথে ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের আনাগোনা।
ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা মান সিংহ ( অনেকে বলেন রাজা বসন্ত রায়) আদি গঙ্গার তীরে একটি ছোট কালী মন্দির নির্মাণ করে দেন।
এরপর ১৫০০ শতাব্দীতে কালীক্ষেত্র দীপিকা নামে একটি বই থেকে জানা যাচ্ছে এই সময়ে কালীঘাটের আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষের বসবাস ছিল। কালীঘাট তখন নানারকম বৃক্ষ ও লতায় আচ্ছন্ন গভীর জঙ্গল। মন্দিরের লাগোয়া একটা সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে সাধু সন্ন্যাসীরা গঙ্গা সাগরে যেত। পরবর্তী সময়ে রাস্তাটির নাম হয় রসা রোড।
আবার ষোড়শ শতাব্দীর(১৫৭৪- ১৬০৪) শেষভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ রয়েছে।।
এই সময়ের যে কিংবদন্তীটি শোনা যায় সেটা হল বর্তমান কালীমন্দিরের কাছেই অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটিরে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করতেন।
একদিন সন্ধ্যে বেলায় তিনি গঙ্গার তীরে বসে সন্ধ্যা বন্দনাদি করছেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা। আগে কখনো এমন আলো তাঁর চোখে পড়ে নি। সেই আলোকে অনুসরণ করে তিনি বর্তমান কালীকুন্ডের কাছে উপস্থিত হলেন।
কালীকুন্ড- তীরে কালীর মুখ এবং পাথরের মত একটি পদাঙ্গুলি দেখতে পান। তারপরেই তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পেলেন, ” যে অঙ্গুলি তুমি পাইয়াছ, তাহা বিষনু কর্তৃক সুদর্শন ছেদিত সতী অঙ্গ। আর ঐ যে কৃষনবর্ণ প্রস্তর ফলক দেখিতে পাইতেছ, তাহা ব্রহ্মার নির্মিত কালীমূর্তি।”
ব্রাহ্মণ এই দৈব বাণী শুনে ঐ উভয় খন্ডকে একত্রিত করে নিত্য পূজা করতে লাগলেন। এরপরে গভীর জঙ্গলের ভেতর নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গও পেলেন।
তারপর থেকে ব্রহ্মচারী প্রস্তরময় সতীঅঙ্গ যত্ন সহকারে সেখানে রেখে প্রতিদিন সেই নির্জন বনে এসে কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজো করতেন। ক্রমে ক্রমে এই জায়গার স্থান মাহাত্ম জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল।
বাংলাদেশে বারো ভুঁইয়ার সময় থেকে কালী পূজোর প্রচলন বেড়ে যায়। এই সময় থেকেই কালীঘাট তীর্থস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।
সাবর্ণ বংশীয় কামদেব ব্রহ্মচারী যিনি মহারাজ মানসিংহের গুরু ছিলেন ও বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের আদিপুরুষ, তাঁর কালীঘাটের বাসস্থান ছিল ‘ফকিরডাঙ্গায়’।
কামদেব ব্রহ্মচারী, ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। প্রতাপাদিত্য সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় কালীক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর কাকা রাজা বসন্ত রায় পরম বৈষনব হয়েও কালীর সেবা ও নিত্যপূজার জন্য তাঁর গুরুদেব ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কে কালীঘাটে পাঠালেন।
এই সময় (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ) কালীঘাট অতি সামান্য অবস্থায় ছিল। রাজা বসন্ত রায় কালীর পর্ণ কুটির ভেঙ্গে একটি ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিলেন।
এখানে কোন আর ইঁটের পাকা বাড়ি ছিল না। চারদিকে বন আর মধ্যে মধ্যে পর্ণ কুটির । ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী এই ক্ষুদ্র কালী মন্দিরে অনেকগুলো শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেগুলো এখনও মায়ের মন্দিরের মধ্যে রয়েছে।
তারপর থেকে ব্রহ্মচারী প্রস্তরময় সতীঅঙ্গ যত্ন সহকারে সেখানে রেখে প্রতিদিন সেই নির্জন বনে এসে কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজো করতেন। ক্রমে ক্রমে এই জায়গার স্থান মাহাত্ম জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল।
কালীর সেবায়েতদের মধ্য ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর নাম প্রথমেই পাওয়া যায়। তাঁর একটি মাত্র কন্যা সন্তান। কালীঘাটের হালদার বংশীয়রা ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র(মেয়ের ঘরের) বংশ।
সাবর্ণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কামদেব ব্রহ্মচারীর হাত ধরে কালীঘাটের কালীমূর্তি লোক সমাজে পরিচিত হল। কামদেবের পুত্র বড়িশার লক্ষীকান্ত মজুমদার সাবর্ণ পরিবারের আদি পুরুষ। পরবর্তীকালে বাংলার নবাবের কাছ থেকে রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন।
এই সময়ে অর্থাৎ ৫০০ বছর আগে কলকাতার প্রাকৃতিক সীমারেখা ছিল- উত্তরে চিৎপুর খাল, দক্ষিণে আদিগঙ্গা, পূবদিকে লবণহ্রদ এবং পশ্চিমে হুগলী নদী। সেই লবণহ্রদের সীমানা আজকের শেয়ালদা, এবং আদি গঙ্গার উত্তর দিকের পাড়ের বিস্তৃতি ছিল আজকের চৌরঙ্গী অবধি।
পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের হাতে যায়। এঁদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায় চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী কালী মন্দিরও তাঁদের সম্পত্তি।
সেই অতীতে চিৎপুর থেকে একটি রাস্তা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা কালীঘাট পর্যন্ত গিয়েছে।
সেকালের এই রাস্তাটি বর্তমান চিৎপুর রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট হয়ে একটা খালের ধারে গিয়ে শেষ হয়। খালটি তখন গোবিন্দপুর ক্রীক নামে পরিচিত ছিল। খাল পেরিয়ে চৌরঙ্গীর জঙ্গল, ভবানীপুর হয়ে রাস্তাটি কালীঘাটে শেষ হয়।
১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক ব্যান্ডেল ছেড়ে সুতালুটিতে চলে এসেছেন। ধীরে ধীরে ইংরেজ পর্তুগীজ সহ অন্যান্য দেশীয়রা কলকাতায় বসবাস শুরু করছে।
তখনও সেকালের সুতালুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের চারদিক ভীষণ জঙ্গলে ঢাকা। একদিকে শেয়ালদা অন্যদিকে হাওড়া ও দক্ষিণে চৌরঙ্গী, কালীঘাট, ভবানীপুর জায়গা কেবলমাত্র খাত, পাঁকে ভরা বাদাতে পরিপূর্ণ।
এরই ভেতরে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তার নির্মাণ শেষ হল।
দুর্গের বিপরীতে কলকাতার ইংরেজদের জন্য তৈরী হল সেন্ট অ্যান’স চার্চ ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে। তার আগেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়ানরা আর্মেনিয়ান চার্চ নির্মাণ করে ফেলেছে।
ইংরেজরা বিশাল বিশাল অট্টালিকা, গির্জা ইত্যাদি নির্মাণ করে কয়েকটি ক্ষুদ্রগ্রামকে শহরে পরিণত করছে। কিন্তু কালীঘাট মন্দির সে সময় বিখ্যাত হলেও তার পুরনো জীর্ণ অবস্থার তখনও সংস্কার হয় নি।
১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত ও নিহত হলেন। রাজা নবকৃষ্ণ ইংরেজদের শুভানুধ্যায়ী ও লর্ড ক্লাইভের পরামর্শদাতা ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক নবকৃষ্ণ এই সময় প্রচুর বিত্তশালী হয়েছিলেন।
১৭৬৫, ১লা আগস্ট দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভ বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেন। নবাবী শাসনের নামমাত্র অস্তিত্ব থাকে । সেই উপলক্ষে রাজা নবকৃষ্ণ মা কালীকে সোনার মুণ্ডমালা দান করেছিলেন।
মা কালী সহ গোটা মন্দির ও মন্দির চত্ত্বরটি গড়ে উঠেছিল মানুষের দানে, শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে।
১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হুজুরিমল বলে এক পাঞ্জাবী বক্সার যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ঠ উপকার করেন। হুজুরিমলের এই সহায়তার জন্য কোম্পানী তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘে জমি প্রার্থনা করলেন। কোম্পানী তাঁর ইচ্ছে পূরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা রাখতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মন্দির সংলগ্ন আদিগঙ্গার ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।
এবার আসি বর্তমান মন্দির নির্মাণের ইতিবৃত্তে।
শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষন পলাশীর যুদ্ধের পর প্রচুর ধনশালী ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়াতে সে কালের কিছু বনেদী ধনী মানুষদের চক্ষুশূল হন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহারাজের প্রতিবেশী চুড়ামণি দত্ত। সব সময়ই তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে টেক্কা দিতে চেষ্টা করতেন।
১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ শে নভেম্বর মহারাজা নবকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যেই মারা যান। সে কালে গঙ্গাতীরে মৃত্যু না হলে লোকে তাকে অপঘাত মৃত্যু বলেই মনে করত। নবকৃষ্ণের মৃত্যুকে লোকে অপঘাতে মৃত্য বলেই মনে করল।
কিছু দিনের মধ্যে প্রয়াত মহারাজের প্রতিবেশী চূড়ামণি দত্ত সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চূড়ামণি বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন।
তিনি তখন রূপোর চতুর্দোলায় বসে গঙ্গাযাত্রায় চললেন। নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসীমালার ঝালর, চারদিকে তুলসী গাছ, আর তার মধ্য চূড়ামণি দত্ত আসন করে বসে আছেন। তাঁর সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরনে রক্তবর্ণের চেলী, পিঠে নামাবলী ও গলায় এবং হাতে জপমালা।
চতুর্দোলাটি নানা ভাবে সাজানো হয়েছে। সামনে পেছনে অসংখ্য লাল পতাকা। অসংখ্য ঢুলি ঢোল বাজাতে বাজাতে চলেছে তাতে বোল উঠছে ‘চূড়া যায় যম জিনতে।’
শোভাযাত্রাটি রাজবাড়ীর সামনে দাঁড়াল। কীর্তনীয়ারা দু হাত তুলে নাচতে নাচতে গাইছে-
“আয়রে আয়- নগরবাসী! দেখবি যদি আয়
জগৎ জিনিয়া চূড়া – যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়া- যম জিনিতে যায়।”
রাজপরিবারের লোকেরা মৃত্যুপথ যাত্রী চূড়ামণি বাবুর এই কঠোর বিদ্রুপে খুব মর্মাহত হলেন। কয়েক দিন গঙ্গাবাস করে, চূড়ামণি দত্ত শেষ পর্যন্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলেন।
পুত্র কালীপ্রসাদ মহাসমারোহে চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন করছেন। এমন সময় নতুন বিভ্রাট উপস্থিত। জনরব উঠেছে কালীপ্রসাদ মাঝে মধ্যেই এক মুসলমান বাঈজীর ঘরে রাত কাটান। সুতরাং তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হবেন না।
কালীপ্রসাদ কায়স্থদের জন্য অত চিন্তিত নন। কারণ রাজা নবকৃষ্ণের অনুগত ছাড়া অন্য কায়স্থদল শ্রাদ্ধকাজে উপস্থিত থাকবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদলের জন্য তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন।
কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা শোভাবাজার রাজবাড়ির বৃত্তিভোগী ও অনুগত। ব্রাহ্মণরা উপস্থিত না থাকলে এবং দান গ্রহণ না করলে কি করে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না।
এই বিপদে পড়ে কালীপ্রসাদ বাবু রামদুলাল সরকারের সাথে পরামর্শ করতে গেলেন। তিনি কায়স্থ সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি।
সরকার মশাই কালীপ্রসাদ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ সন্তোষ রায়ের কাছে। বরিষার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় তৎকালীন কলকাতার হিন্দু সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।
রামদুলাল বাবুর মুখে সব ঘটনা শুনে, সন্তোষ রায় কালীপ্রসাদ বাবুকে অভয় দিয়ে জানালেন তিনি ব্রাহ্মণদল নিয়ে তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকবেন।
শ্রাদ্ধের দিন তিনি বড়িশা, সরশুনা, কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের নিয়ে শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হলেন। শ্রাদ্ধের ক্রিয়া কর্মাদি মিটে গেলে কালীপ্রসাদ দত্ত ব্রাহ্মণদের সম্মানার্থে ২৫০০০/- টাকা বিদায় স্বরূপ সন্তোষ রায়ের হাতে দিলেন।
সন্তোষ রায় তখন ব্রাহ্মণদের বললেন, ” দেখুন, আমরা যদি এই টাকা নিই তাহলে লোকে বলবে যে আমরা টাকার লোভে এক সমাজ পতিত ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলাম। এই অপবাদের ভাগীদার হওয়ার চেয়ে এই টাকা ধর্ম কাজে ব্যয় করলে কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না।” সন্তোষ রায়ের যুক্তিযুক্ত কথাকে সবাই একবাক্যে সমর্থন করল।
সেই সময় কালীঘাট মন্দিরে ভক্তসমাগম অনেক বেড়ে গিয়েছে কিন্তু মন্দিরের ভগ্নদশা। মন্দিরের নব নির্মান দরকার। সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদের সাথে নিয়ে কালীপ্রসাদ দত্তের দানকৃত টাকায় কালীর মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নতুন মন্দির নির্মাণের আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামনাম রায় এবং ভাইপো রাজীবলোচন রায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। বর্তমান এই মন্দিরটি নব্বই ফুট উঁচু। এটি নির্মাণ করতে আট বছর সময় লেগেছিল এবং খরচ হয়েছিল ৩০,০০০/- টাকা।
মন্দির সংলগ্ন জমিটির মোট আয়তন ১ বিঘে ১১ কাঠা ৩ ছটাক; বঙ্গীয় আটচালা স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মূল মন্দিরটির আয়তন অবশ্য মাত্র ৮ কাঠা।
কালীঘাট কালীমন্দিরের কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিটি অভিনব রীতিতে নির্মিত। মূর্তিটির জিভ, দাঁত ও মুকুট সোনার। হাত ও মুণ্ডমালাটিও সোনার।
দেবী মায়ের সোনার জিভ গড়িয়ে দিয়েছিলেন পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। পাতিয়ালার মহারাজও সোনার মুণ্ডমালা দান করেন। খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল কালী মায়ের চার হাত রুপোর তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই হাত পরে সোনার করে দিয়েছিলেন কালীচরণ মল্লিক। দেবীর মাথার ছাতা দান করেছিলেন নেপালের সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর।
মূল মন্দির সংলগ্ন অনেকগুলি ছোটো ছোটো মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি দেবতা পূজিত হন।কালীঘাট মন্দিরের নিকটেই পীঠরক্ষক দেবতা নকুলেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দির সংলগ্ন যে পুকুরটি দেখতে পাওয়া যায় সেটাই নাকি পুরাকালের কালীকুন্ড। যার সাথে আদি গঙ্গার যোগ ছিল।
জনপ্রবাদ এই কুন্ড পারেই নাকি সতীর প্রস্থরবৎ পায়ের আঙুল পাওয়া যায়। মন্দিরে মধ্যে একটি সিন্দুকে সতীর প্রস্তরীভূত অঙ্গটি রক্ষিত আছে; এটি কারোর সামনে বের করা হয় না।
এরই মধ্যে কলকাতায় পর্তুগিজদের পর্তুগিজ চার্চ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়ে গেছে। সে সময়ে কলকাতা শহরে কোন মসজিদ দেখা যায় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ভোসরি শাহ মসজিদ বলে উত্তর কলকাতার কাশীপুর লকগেটের কাছে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠত হয়।
১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কালীঘাট মন্দির একটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন ইতালীর শিল্পী Gaetano Zancon ।
শোনা যায়, এই মন্দিরে কেবল রাজা-জমিদার বা ভক্তরাই নন, পুজো দিয়েছেন ইংরেজ সাহেবরাও। একটি মামলা জেতার জন্য একবার মানত করে গিয়েছিলেন একজন সাহেব। তার পর সেই মামলা জেতার পর এই মন্দিরে এসে তখনকার সময়ে তিন হাজার টাকার পুজো দিয়েছিলেন তিনি।
পঞ্জাব ও বার্মা দখলের পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এই মন্দিরে ষোড়শ উপাচারে পুজো দেওয়া হয়েছিল।
আবার শুধু ইংরেজরাই নয়। ওয়ার্ড লিখেছেন, প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ’শ জন মুসলমান এখানে পুজো দিয়ে যেতেন।
কালীঘাটে মূল পুজো আটটি- রক্ষাকালী, স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, মনসাপুজো, দুর্গাপুজো, শীতলাপুজো, চড়ক ও গাজন এবং রামনবমী।
কালীঘাটে কালীপুজোর রাতে দেবীকে কালীরূপে নয়, লক্ষ্মীরূপে আরাধনা করা হয়। কালীঘাটের এই লক্ষ্মীপুজো মহালক্ষ্মী পুজো নামেও খ্যাত। এর আর এক নাম শ্যামা লক্ষ্মীপুজো।
অলক্ষ্মীকে গোবরের পুতুল মতো করে মূল মন্দিরের বাইরে রাখা হয়। তারপর মন্দিরের সেবায়েত হালদার বংশের সকলকে লক্ষ্মীপুজোয় অংশগ্রহণ করতে হয়।
কালীঘাটে বামাচারী কাপালিক ও অঘোরপন্থীদের দাপটের সময় কালীপুজোর রাতে লক্ষ্মীপুজো বলে কিছু ছিল না। শুধু কালীপুজোই হত। কালীঘাটে যুগযুগান্ত ধরে কালীপুজোর রাতে কালীপুজোই হয়ে এসেছে।
মন্দিরের সমস্ত ক্ষমতা ভবানীদাস চক্রবর্তীর হাতে আসার পর তিনিই কালীপুজোর রাতে বিশেষ কালীপুজো বন্ধ করে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজোর প্রবর্তন করেন।
কালীঘাটে কালীপুজোর দিন মায়ের মন্দিরে লক্ষ্মীপুজোর সময় কিন্তু কোনও ঘটস্থাপন হয় না। শুধু লক্ষ্মীপুজো কেন, কোনও পুজো উপলক্ষেই এখানে ঘট স্থাপনের নিয়ম নেই। কারণ, মা স্বয়ং এখানে বিরাজমান।
অলক্ষ্মী বিদায়ের পরই হাত-পা ধুয়ে পুরোহিত শ্যামা লক্ষ্মীপুজোয় বসবেন। প্রত্যেক সেবায়েত-পরিবার থেকে মা লক্ষ্মীর জন্য নিরামিষ ভোগ আসবে মন্দিরে। সেই ভোগ থরে থরে সাজানো হবে মা দক্ষিণা কালীর সামনেই। লক্ষ্মীর জন্য নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণা কালীর জন্যও তো আলাদা ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে।
সেই ভোগ কিন্তু আমিষ। তাতে মাছ-মাংস সবরকম থাকবে। মা কালীর আমিষ ভোগও মায়ের সামনেই সাজানো হবে।
তবে লক্ষ্মীর নিরামিষ ভোগের সঙ্গে যেন কোনওভাবেই মা কালীর আমিষ ভোগের ছোঁয়া না লাগে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি, কালীঘাটে মহালক্ষ্মী পুজোর দিনও কিন্তু পাঁঠাবলি হয়।
সেবায়েত পরিবারের লোকজন ও পশ্চিমবঙ্গীয়দের পাঁঠাবলি নেই। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় যাঁরা তাঁরাও তো এদিন মায়ের কাছে আসতে পারেন। মায়ের নামে সংকল্প করে তাঁরা পাঁঠাবলিও দেন।
কালীঘাটে মায়ের দর্শনের সময় ভোর ৫টা – বেলা ২ টো। এবং বিকেল ৫ টা – রাত্রি ১০.৩০।